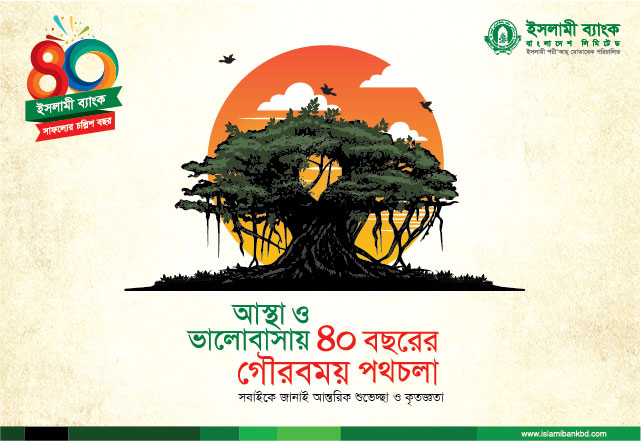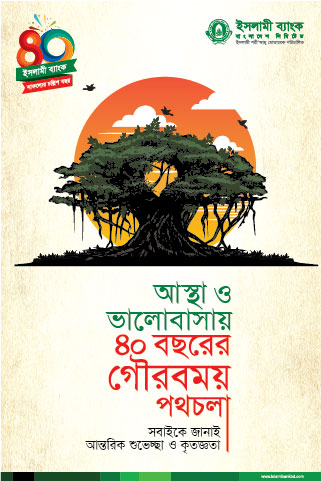ইসরাইলি নাৎসি কৌশল, আইনস্টাইনের চিঠি ও নেতানিয়াহুর ‘আরব ফ্যান্টাসি’
- ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম
- ২৫ মে ২০২৪, ০০:০০
(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)
উত্তরাধিকার সূত্রে মধ্যপ্রাচ্যের মূল বিষয়গুলো
ইউরোপে ইহুদি নিধনযজ্ঞে সৃষ্ট ‘দরদ’ থেকে ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় গৃহীত বিভাজন পরিকল্পনার ফলে ইসরাইল নামে রাষ্ট্রের জন্ম। আসলে এটি হচ্ছে গল্পের ছোট একটি অংশমাত্র। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, ফিলিস্তিনের ৫৬ শতাংশ ভূখণ্ডজুড়ে ইহুদি রাষ্ট্র; ৪২ শতাংশজুড়ে আরব রাষ্ট্র এবং ‘জেরুসালেম ও আশপাশের ২ শতাংশ মিলে একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল হবে। প্রস্তাবে ডিক্রি জারি করা হয় যে, ইহুদি রাষ্ট্রে বসবাসকারী আরবরা সেখানেই বসবাস অব্যাহত রাখবে এবং জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী সব রকম মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্রিটিশরা যেতে না যেতেই ৭৭ শতাংশ ভূখণ্ড ইসরাইলিরা দখল করে নেয়।’
১৯৬৭ সালে ইসরাইল কতিপয় আরব রাষ্ট্রের বিশাল এলাকা দখল করে। ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের ১৯৬৯-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ইসরাইল। তারা সব সময়ই দাবি করে আসছে যে, ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের পরপরই ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে আরব সৈন্যদের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়।
মূলোৎপাটন ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত
ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্ঘাতের মূল বিষয় হচ্ছে, একটি পুরো জাতিকে উৎখাত ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ইহুদিদের স্থান করে দেয়া। ‘ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় বিশুদ্ধ রূপে উৎসাহিত হয়নি; বরং তা ‘ইহুদিবাদ’-এর রাজনৈতিক উচ্চাকাক্সক্ষা পূরণের লক্ষ্যে অর্জন করা হয়েছে।’
Jews for Justice in the Middle East তাদের প্রকাশনা ‘ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্বের মূল’ শীর্ষক বইতে লিখেছে, ‘মধ্যপ্রাচ্যে রক্তপাতের যে ধারাবাহিকতা তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান, তার মূল কারণ খুঁজে পাওয়ার মধ্যে নিহিত। আমাদের অবস্থান হলো, ফিলিস্তিনিদের সত্যিকার দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। শত বছর ধরে তাদের মাতৃভূমি জবরদখল করা হয়েছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের সময় এবং উভয়পক্ষের পরবর্তী সব অপরাধের মূল কারণ- অবশ্যই এই আসল অবিচার থেকে উৎসারিত।’
ইহুদিদের ভোগান্তি-ইহুদিবাদী অবিচারের যৌক্তিকতা
ইউরোপে ইহুদি হত্যাযজ্ঞকে ইহুদিবাদের জন্মের পক্ষে একটি যুক্তি হিসেবে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। ইসরাইলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রফেসর বেনজামিন বেইট-হাল্লাহমি ‘Original Sins: Some Reflectios on the History of Zionism’-শীর্ষক একটি বই লিখেন। বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘ফিলিস্তিনি যারা প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে তারা কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিদের ওপর নির্যাতনকারী ছিল না। ইহুদিদেরকে তারা বন্দীখানায় প্রেরণ কিংবা হলুদ টুপি পরতেও বাধ্য করেনি। তারা ধ্বংসযজ্ঞের (holocaust) ষড়ষন্ত্রও করেনি। তবে তাদের একটি অপরাধ ছিল- সত্যিকারের সামরিক ক্ষেত্রে তারা ছিল দুর্বল ও প্রতিরক্ষাহীন। সুতরাং কাল্পনিক প্রতিশোধের নিছক শিকার হলো তারা...।’ নির্যাতনকারীদের পক্ষের একজন বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি ন্যায়বিচার ও মানবিক আচরণের অত্যাবশ্যকীয় দাবি তোলার কথা এই বইটিতেই দেখা যায়।
এন্টিসেমিটিজম : অপর যৌক্তিকতা
ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের নীতিমালার কোনো সমালোচনা শুনলেই অনেক ইহুদিকে অভিযোগ করতে শোনা যায়, ইসরাইল ইহুদিবিদ্বেষী প্রচারণার শিকার যাকে তারা বলতে চায় ‘Anti-Semitism’ বা সেমিটিক জনগোষ্ঠীবিরোধী।
সত্যিকার অর্থে সিমিটিয়রা (Semites) সেমিটিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সদস্য, যাদের মধ্যে রয়েছে নিকটপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, আরব, আর্মেনীয়, ব্যাবিলনের বাসিন্দারা, কার্থাজিনিয়ান, ইথিওপিয়ান, হিব্র্রুভাষী ও ফিনিসিয়ানরা। সুতরাং ইহুদিরা বিশ্বের একমাত্র সেমিটিক নয়, নয় পবিত্র ভূমিতেও।
ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত আগে সুদীর্ঘ ১৮১৩ বছর ধরে যারা পবিত্র ভূমির আদিবাসী হিসেবে পরিচিত সেই ফিলিস্তিনিরা সবাই আরব ও সেমিটিক। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরো ২২টি আরব জাতি যাদেরকে ইসরাইলের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারাও সেমিটিক।
অন্য অনেকের মতো যারা ‘এন্টি-সেমিটিক’ শব্দবদ্ধকে ‘ইহুদি-বিদ্বেষ’ অর্থে ব্যবহার করে আসছে, ইসরাইলের পক্ষ নেয়া সে সব লোক বুঝতেই পারে না যে, ইসরাইলের কোনো সমালোচনাই কেবল জাতি-গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা থেকে উৎসারিত নয়। পবিত্র ভূমিতে ইসরাইল ফিলিস্তিনি সেমিটিকদের ওপর একটি বর্ণবাদী ও বর্ণবিদ্বেষী নির্যাতন চালিয়ে আসছে।
বেইট-হাল্লাহমির মতে, ইহুদিবাদের সমস্যা শুরু হয় যখন এটি ফিলিস্তিনের জমিতে আবির্ভূত হয়। সেখানে তা হয়ে দাঁড়ায় একটি ইচ্ছাকৃত উপনিবেশ, যা বরাবরই একটি জাতির বিরুদ্ধে তার সম্পদ থেকে উৎখাতকরণ ও শিকারে পরিণত’ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখে।’
নেতানিয়াহুর চোখে ‘আরব ফ্যান্টাসি’
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মি নেতানিয়াহুকে অনেক বিশ্লেষকই মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার পথে অন্যতম ‘বাধা সৃষ্টিকারী’ বিবেচনা করছেন। তিনি ‘A durable peace: Israel and its place among nations’ শীর্ষক একটি বই লিখেন যেখানে তিনি ফিলিস্তিনিদের কিছু প্রধান দাবিকে নিছক আরবদের অলীক কল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, আরব কল্পনা দু’টি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত :
ক. ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদেরকে তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে আসার অধিকার বাস্তবায়ন এবং
খ. জেরুসালেমের পুনঃবিভক্তি নিছকই একটি কল্পনা।
এখনো আরব ও অন্যান্য জাতি এরকম একটি কল্পলোকে ঝুলে আছে।
আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্য শান্তির দূতিয়ালি করছিল তখন নেতানিয়াহু আমেরিকা ও পশ্চিমের তীব্র সমালোচনা করেন তাদের ভূমিকার জন্য। ‘স্বভূমে ফিরে আসার অধিকার বাস্তবায়ন’ নামক আরব কল্পনার ব্যাপারে আমেরিকার সরাসরি না বলতে পারার তিনি সমালোচনা করেন। জাতিসঙ্ঘের ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের কথা রয়েছে। কিন্তু এই চরম-ডানপন্থী রাজনীতিক এ প্রস্তাব মানতে পারেননি এবং যুক্তরাষ্ট্র যাতে এ প্রস্তাবটিকে পরিত্যাগ করে সে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তার বইতে তিনি উল্লেখ করেন, এখনো যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব সমর্থন করে কি না- এ প্রশ্নে এক কথায় ‘না’ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারেনি; বরং তারা তিন দিন ধরে তোতলাতে তোতলাতে এক ধরনের দ্বিধার প্রকাশ করল। নেতানিয়াহু মনে করেন, এই অস্পষ্ট ও পরোক্ষ অবস্থান আরবদের মনে কোনো একদিন ইসরাইলকে চেপে ধরার আশা সঞ্চার করবে। এর ফলে ইসরাইল-সীমান্তে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী আরব শরণার্থীদের একদিন হয়তো ইসরাইলে নিতে হবে। নেতানিয়াহুর মতে, শরণার্থী ইস্যুটি অন্যায়ভাবে নেয়া জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাবের মতোই সেকেলে একটি বিষয় (যেমন- ১৯৪৭ সালে ইসরাইলের দখলে থাকা ভূমির ৫০ শতাংশ বরাদ্দের বিভাজন পরিকল্পনা এবং জেরুসালেমের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রস্তাব)। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ‘তাদের আনুষ্ঠানিক অবস্থান অবশ্যই বদলাতে হবে এবং সাদামাটা কথায় এ প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিতে হবে।’
ভারসাম্যহীনতা-অবিচারের লক্ষণ
নিজেদের ভূমিতে বসবাসের অধিকার পেতে সংগ্রামরত ফিলিস্তিনিদের বিষয়টি সঠিক প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করতে হবে। তাদের প্রকৃত অর্থে তেমন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা বিমানবাহিনী নেই। তার পরও তারা লড়াই করছে- তাদের লড়াই হলো বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সামরিক শক্তির বিপক্ষে যা আবার একমাত্র বৃহৎশক্তির মদদপুষ্ট।
ফিলিস্তিনিরা প্রতিদিনই দখলদার শক্তির হাতে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে। অধ্যাপক চমস্কি তার মন্তব্যে কথাটি এভাবে তুলে ধরেছেন, ‘আরব-বিরোধী বর্ণবাদ... এতই বিস্তৃত যে, তা দৃষ্টির অগোচরে রয়ে যায়, সম্ভবত এটি বর্ণবাদের সেই ধরন যাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।’ বর্ণবাদের ব্যাপারে বিশ্ব নেতাদের বাছাইকৃত কিছু মন্তব্য সযত্ন পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিশ্বের প্রায় সবখানেই দ্বৈতনীতির যে প্রকোপ পরিলক্ষিত হয় তা সত্যিই ভাবার বিষয়। পিটারসন এ ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা মর্মস্পর্শী।
তিনি লিখেন :
‘ইসরাইলিরা খুন হলে জোরেশোরে তার নিন্দা করা হয়, অপর দিকে যখন কোনো ফিলিস্তিনি খুন হয় তখনো নিন্দা হয়, তবে জোরালোভাবে নয়। ফিলিস্তিনিদের খুনকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের আত্মরক্ষামূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপর দিকে, অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মোকাবেলার বৈধ অধিকার এবং অনুরূপ আত্মরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুল্লেখ্য থেকে যায়। তাহলে, ভারসাম্য কোথায়?... ফিলিস্তিনিরা যখন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় তখন গ্রাহাম (কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান। জেরুসালেমে বোমা ফাটলে অনুরূপ আহ্বান শোনা যায়নি।’
জাতিসঙ্ঘের অত্যন্ত সম্মানিত সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান। দু’টি মারাত্মক ঘটনায়- জেরুসালেমে বোমা হামলা এবং হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী আধ্যাত্মিক নেতা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার দেয়া তার বক্তব্য চোখ খুলে দেয়ার মতো।
জেরুসালেমে বোমা হামলা : ‘পরিকল্পিতভাবে বেসামরিক লোকজনকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হায়েনার মতো একটি কাজ এবং কোনোভাবেই এটিকে যৌক্তিক মনে করা যায় না। আমরা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই, যারা এ ধরনের অপরাধের পরিকল্পনা, মদদ ও বাস্তবায়ন করে, তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে।’
শেখ ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ড: ‘এ ধরনের কর্মকাণ্ড কেবল আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী নয়; বরং এ সবের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সন্ধানে কোনো সাহায্য সম্ভব নয়। আমি এ এলাকার প্রত্যেককেই শান্ত থাকার এবং সর্ব প্রকার সহিংসতা ও বাড়াবাড়ি এড়িয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই।’
সঙ্ঘাতের পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন
মধ্যপ্রাচ্য সঙ্ঘাতের প্রতিবেদনে প্রায়ই ইসরাইলের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। এ প্রবণতাটি আমেরিকায় ব্যাপক। অপরদিকে ব্রিটিশ মিডিয়াগুলোও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই।
মার্কিন মিডিয়া: আমেরিকার সরকার ও মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাস বিষয়ে যে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে সে ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাঈদ The Progressive (৩০ মে, ১৯৯৬) এ বলেন, ইসরাইল রাষ্ট্রটি আশপাশের রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাপক হানা দিয়েছে, বোমা হামলা করেছে, ইচ্ছামতো ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। সম্প্রতি এটি সব ধরনের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনি এলাকায় দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। এসব কার্যকলাপ ‘ইসলামী সন্ত্রাস’কে বারবার উসকে দিচ্ছে। এ বিষয় এবং ‘ইসরাইলের ইতিহাস ও এর চরিত্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আমেরিকার মিডিয়ায় কিংবা সরকারি আলোচনার কোথাও উল্লিখিত হয় না।
এবিসি, সিবিএস ও এনবিসি ফিলিস্তিনি নিহতদের তুলনায় ইসরাইলি নিহতদের ব্যাপারে ৩ থেকে ৪.৪ গুণ কাভারেজ প্রদান করে।
অপর এক প্রতিবেদন অনুসারে, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার জন্য ইসরাইলের পক্ষের গ্রুপগুলো কৌশলে ব্যাপক চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে প্রধান প্রধান মিডিয়াগুলোকে বয়কট করা, প্রচুর ফোনসহ ইমেইল, পত্রিকায় চিঠি প্রেরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইউএসের জাতীয়ভিত্তিক ও ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক জাতীয় সরকারি বেতার ন্যায়পাল জেফরি ভরকিন বলেন, ‘ইতঃপূর্বে কেউ এ ধরনের কোনো চাপ কখনো দেখেনি।’
ব্রিটিশ মিডিয়া : গ্লাসেগা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া ইউনিটের অধ্যাপক গ্রেগ ফিলো মধ্যপ্রাচ্য সঙ্ঘাতের টিভি সংবাদ পরিবেশনার উপর একটি গবেষণা চালান। এ জরিপে দেখা যায় ইসরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্ঘাতের টিভি সংবাদগুলো দর্শকদের বিভ্রান্ত করে এবং সেখানে ইসরাইলের সরকারি মতামতের প্রতিফলন ঘটে। ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরাইলি পক্ষকে কমপক্ষে দ্বিগুণ সময় ধরে উদ্ধৃত করা হয় আবার দুই পক্ষকে উপস্থাপনের সময়কার ভাষা ও ভাষ্যও হয় ভিন্নতর। এগুলো ইসরাইলিদের পক্ষে কাজ করে এবং দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। এই গবেষণার ফলাফল ‘Bad News from Israel’ নামক বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে- জনমত তৈরিতে টিভি সংবাদের গুরুত্ব কতটুকু। আজকাল ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্ঘাতের বিষয়ে ৮০ শতাংশ লোকের তথ্যের সূত্র টিভি সংবাদ। ‘এর পরও তারা যা দেখে ও শুনে তার মান এতই বিভ্রান্তিমূলক ও আংশিক যে তা থেকে এই সঙ্ঘাতের গ্রহণযোগ্য কারণ ও এর সমাধানে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব।’
লেখক: গবেষক
আরো সংবাদ
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা