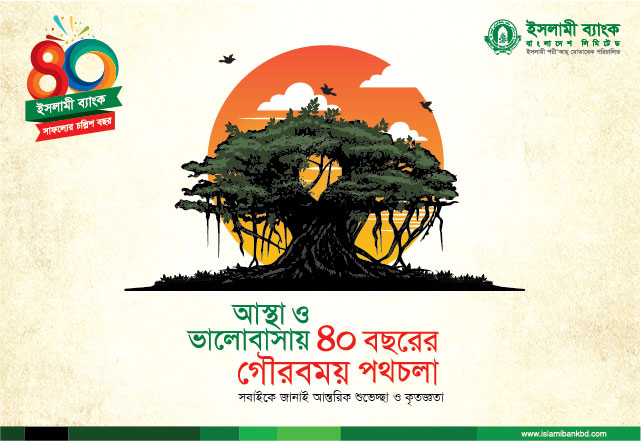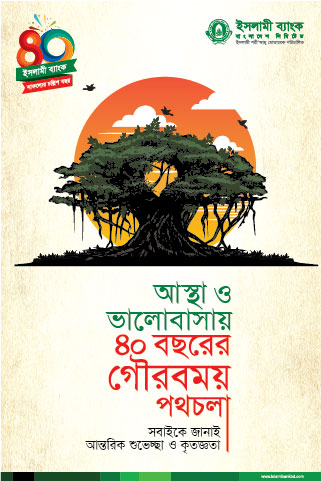অগ্নিবীণা কাব্য পাঠের ভূমিকা
- আবু হেনা আবদুল আউয়াল
- ২৪ মে ২০২৪, ০০:০৫
কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য-আকাশে সূর্যোজ্জ্বল প্রতিভা নক্ষত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আশা-নিরাশা ও নব্য ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যে তার দৃষ্টিকাড়া আবির্ভাব। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনীতি ও সাংবাদিকতার সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হন; উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক গণজাগরণ, যে জাগরণের মধ্যদিয়ে উপনিবেশ ও সামন্ত শাসন-শোষণ থেকে দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তি। এ মুক্তি আকাক্সক্ষার পটভূমিতে রচিত হয়েছে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নি-বীণা’র কবিতাসমষ্টি। এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও বিষয়ভাবনা ও শিল্পের নৈপুণ্যে এবং স্বাতন্ত্র্যে ও মৌলিকত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ, শুধু নজরুল-সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও, এমনকি বিশ্ব সাহিত্যেও। এতে উৎকীর্ণ হয়েছে তার কাল ও কালোত্তীর্ণ কাব্যপ্রতিভার গাঢ়রং স্বাক্ষর।
প্রথম সংখ্যা থেকে (‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের বেশ পূর্ব থেকেই) অর্ধ সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ছাপাতে থাকে। আবার প্রকাশের পরও তা অব্যাহত থাকে। এ বিজ্ঞাপনে ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে এ রকম কবিতা ও গানের নাম উল্লিখিত হয়। তাতে লেখা হয়- এতে থাকবে কবির আজতক লেখা সমস্ত গরম কবিতা ও গান। যেমন, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’, ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘ধূমকেতু’, ‘আনোয়ার’, ‘কোর্ব্বানী’, ‘মোহরম’, ‘শাতিল আরব’, ‘রণ-ভেরী’, ‘আনোয়ার’, ‘আগমনী’ প্রভৃতি কবিতা এবং ‘বন্দী-বন্দনা’, ‘মরণ-বরণ’, ‘জাগরণী’, ‘অমরমন্ত্র’, ‘ভাঙার গান’ প্রভৃতি গান। সঙ্গে সঙ্গে তাগিদ দেয়া হয় বইটি পেতে চিঠি লিখে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে বা টাকা পাঠিয়ে দিতে। সতর্ক করে লেখা হয়, ‘বিলম্বে হতাশ হতে হবে’।
পরে ‘অগ্নি-বীণা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে দেখা যায়, এতে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত গানগুলো বাদ পড়েছে, শুধু কবিতা-গরম কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে। নজরুল গ্রন্থের ‘মুখবন্ধ’-এ এ জন্য তার অনভিজ্ঞতা ও পরবর্তী পরিকল্পনাসহ নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সেই মুখবন্ধটি উদ্ধৃত হলো- অগ্নি-বীণা’র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং এঁকেছেন তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রী বীরেশ্বর সেন। এ জন্য প্রথমেই তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।
‘ধূমকেতু’র পুচ্ছ জড়িয়ে পড়ার দরুন যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি করে ‘অগ্নি-বীণা’ বের করতে পারলাম না। অনেক ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। সর্বপ্রথম অসম্পূর্ণতা যেসব গান ও কবিতা দেবো বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেইগুলো দিতে পারলাম না, কেননা সে সমস্তগুলো দিতে গেলে বইটি খুব বড় হয়ে যায়, তারপর ছাপানো ইত্যাদি খরচ এত বেশি পড়ে যায় যে, এক টাকায় বই দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। পূর্বে যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তখন ভাবিনি যে, সমস্ত কবিতা-গান ছাপতে গেলে তা এত বড় হয়ে যাবে। কেননা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোনো দিনই ছিল না, আজও নেই। এর জন্য যতটুকু গালি-গালাজ বদনাম সব আমাকে অকুতোভয়ে হজম করতে হবেই। তবু আমার পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার এই ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। বাকি কবিতা ও গানগুলো দিয়ে এবং পরে কতকগুলো কবিতার সমষ্টি নিয়ে এই রকম আকারের ‘অগ্নি-বীণা’র দ্বিতীয় খণ্ড দিন পনরের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। আর্য্য পাবলিশিং হাউজের ম্যানেজার আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহের ঐকান্তিক চেষ্টারই সাহায্যে আমি ‘অগ্নি-বীণা’ কোনো রকমে শেষ করতে পারলাম; আরো অনেকে অনেকরকম সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
বিনীত কাজী নজরুল ইসলাম।
মুখবন্ধে উল্লিখিত পরিকল্পনা বা ঘোষণা অনুযায়ী ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আর বের হয়নি। তৎপরিবর্তে পরে ‘বিষের বাঁশী’ (আগস্ট, ১৯২৪) কাব্যগ্রন্থ বের হয়। তাতে দু-চারটি কবিতা ছাড়া সবগুলোই ছিল গান-উদ্দীপনাধর্মী গান।
‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের শেষার্ধে, যা গোয়েন্দা দপ্তরে পৌঁছে ২৫ অক্টোবর। কলকাতার ৭, প্রতাপ চাতুর্য্যে লেনের আর্য্য পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। এটি ছাপা হয় কলকাতার মেটকাফ প্রেসে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৬৬; দাম এক টাকা মাত্র। (মুজফ্ফর আহ্মদ, ২০১৫: ১৭৬)। উল্লেখ্য, আর্য্য পাবলিশিং হাউসের মালিক ছিলেন অরবিন্দ কুমার ঘোষ। তার পরিচালক শরৎচন্দ্র গুহের প্রস্তাবে ও উৎসাহে আর্য্য পাবলিশিং হাউস থেকে নজরুল তার গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হন। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, ‘অগ্নি-বীণা’ ও ‘যুগবাণী’র প্রথম প্রকাশক আর্য্য পাবলিশিং হাউস হলেও প্রথম মুদ্রণের সময়ে তারা প্রকাশক হিসাবে নিজেদের নাম ছাপাননি। মামলা-মোকদ্দমা হয়ে যেতে পারে এই ভয় তাদের মনে ছিল। কাজেই, প্রথম বারে কলকাতা, ৭ নম্বর প্রতাপ চাতুর্য্যে লেন হতে কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই বাহ্যতঃ পুস্তক দু’খানার প্রকাশকও হয়েছিল।’ (ঐ, ১৭৮)
‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থ বের হওয়ার সাথে সাথে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ ষোড়শ সংখ্যায় (২৪ অক্টোবর, ১৯২২) বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, তাতে লেখা হয়, ধূমকেতু-সারথি ‘বিদ্রোহী’র সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর কবিতার বই ‘অগ্নি-বীণা’ বের হলো। কাজীর ফটোসহ সুদৃশ্য বাঁধাই- দাম এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান : আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা।
মুজফ্ফর আহমদের ভাষ্য থেকে জানা যায়, ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থ প্রথমবার ২২০০ কপি ছাপা হয়, তা এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়। কাজেই বছর না যেতেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। তখন নজরুল জেলে। এ সংস্করণেও সমপরিমাণ কপি ছাপা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, ‘অগ্নি-বীণা’ কী দারুণ সাড়া ফেলেছিল বাঙালি পাঠক সমাজে। পরবর্তীকালে নজরুল ডি. এম. লাইব্রেরির কাছে দুই হাজার টাকায় ‘অগ্নি-বীণা’র স্বত্ব বিক্রয় করে দেন।
প্রকাশের পর বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় (১৩২৯/১৯২২) ‘অগ্নি-বীণা’র পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখে-
এতদিন বাংলার কাব্যকুঞ্জে প্রেমের কবিতাই অজস্র ফুটিত, বীর-বীণার ঝঙ্কার ক্বচিৎ শুনা যাইত। কিন্তু ‘অগ্নি-বীণা’র প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্বব্যঞ্জক মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। নৃত্যদোদুল ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গিমা বিকাশে কবি অপূর্ব গুণপনা দেখাইয়াছেন। কবি বাঙালি পল্টনে হাবিলদারের কাজ করিয়া যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন ‘কামাল পাশা’ কবিতায় তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে,- বাংলা সাহিত্যে ইহা একেবারে অভিনব জিনিস। কবির এই বীর ভাব অনেক কবিতাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া কবি যেসব অনুপম উপমা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। জাতীয় জাগরণের দিনে ‘অগ্নি-বীণা’র বীরোদাত্ত বাণী বাঙালি জাতি আদরের সহিত গ্রহণ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস। ... কবি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রচ্ছদখানি পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।
এ কাব্যগ্রন্থে শব্দ ব্যবহারেও তার স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব ও শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার এ ব্যবহার কৃত্রিম বা আরোপিত মনে হয়নি সৃষ্টিশীলতা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের কারণেই; আবার হাইফেনযোগে তিনি অনেক শব্দের যৌগিকীকরণ করেছেন, যাতে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে।
অন্য দিকে ছন্দের মাত্রা ও ধ্বনি স্পষ্টীকরণের জন্য প্রচুর হসন্তও ব্যবহার করেছেন তিনি। এ ছাড়াও তিনি প্রচুর, কমা, ঊর্ধ্বকমা ও আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন এবং সে সঙ্গে কখনো কখনো ডাবল আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ও দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন ভাব স্পষ্ট করার প্রয়োজনে।
যেমন, ১. যৌগিকীকরণে হাইফেন : আমি অবমানিতের মরণ-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের! ২. হসন্ত ও ডবল আশ্চর্যবোধক চিহ্ন : তোরা সব জয়ধ্বনি র্ক!
তোরা সব জয়ধ্বনি র্ক !! ৩. কমা : আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি! আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান, ৪. ঊর্ধ্বকমা : প্রলয় ব’য়েও আসছে হেসে’- ভেঙে আবার গ’ড়তে পারে সে চির-সুন্দর! এসব কারণে বলা যায়, তিনি এ কাব্যগ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র কাব্যভাষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা একজন কবির সহজ শনাক্তযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থে ছন্দ ব্যবহারেও তার স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রলয়োল্লাস’ ও ‘কামাল পাশা’ স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। অন্য কবিতাগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, কিন্তু নিরূপিত বা অতি প্রচলিত পর্ব, পর্বাঙ্গ ও মাত্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।
‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয় বিদ্রোহ-বিপ্লব ও সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি এবং এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক দুঃশাসন ও দেশীয় সামন্ত শোষণ থেকে মুক্তির উদগ্র স্বপ্নাকাক্সক্ষা। এর প্রতিটি কবিতায়ই নানাভাবে তা মর্মরিত। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নানা কালাকানুন জারি করে, বাড়িয়ে দেয় নির্যাতন, নিপীড়ন, জেল-জুলুম, হত্যাযজ্ঞ। যুদ্ধকালে দেয়া প্রতিশ্র“তি ভঙ্গ করে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ শাসন, তুরস্ক ভূ-খণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার অপচেষ্টা, জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কারণে ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলমান মিলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ দুই আন্দোলন চলছিল অভিন্ন ধারায় ও গতিস্পন্দে। এ ঊর্মিময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লেখা। নানা উপমা-রূপকে, চিত্র-চিত্রকল্পে, মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যে, কিংবদন্তি ও ইতিহাসের প্রসঙ্গে-চরিত্রে নজরুল পরাধীনতা, শোষণ-বঞ্চনা ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে অথচ শিল্পিত সুরে-স্বরে উচ্চারণ করেছেন জনগণ মুক্তির বাণী। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিকে যদি ‘অগ্নি-বীণা’র মূল ভাবের কবিতা বলি, তাহলে অন্য কবিতাগুলো ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সম্পূরক ভাবের কবিতা নির্দ্বিধায় বলা যায়।
পুরাতন সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সৃষ্টির দুর্মর আকাক্সক্ষা ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়; অসুন্দর, পুরাতন ও জীর্ণতা ধ্বংস করে তৎস্থলে নতুন সুষ্টি করবে নতুন যুগের তরুণরা; ধ্বংস তো সৃষ্টির জন্যই, তাতে ভয় পেলে চলবে না, তাঁর ভাষায়,
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন! / আসছে নবীন-জীবন-হারা অসুন্দরের করতে ছেদন! / তাই সে এমন কেশে দেশে / প্রলয় বয়েও আসছে হেসে- / মধুর হেসে। / ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর! (প্রলয়োল্লাস)
শিব ও দুর্গা-এ দু’পৌরাণিক চরিত্র ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘বিদ্রোহী’, ‘ধূমকেতু’, ‘আগমনী’ ও ‘রক্তাম্বরধারিণী মা’ কবিতায় নানাভাবে ধ্বংস ও সৃষ্টির দ্বৈত অনুষঙ্গে উল্লিখিত; অন্যান্য পৌরাণিক চরিত্রও একই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত, যেমন,
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার, / নিঃক্ষত্রিয় কবির বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার! / আমি হল বলরাম-স্বন্ধে, / আমি উপাড়ি’ ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে সৃষ্টির মহানন্দে! (‘বিদ্রোহী’)
‘রক্তাম্বরধারণী মা’ কবিতাটিতেও দুর্গাকে আহ্বান করেছেন ধ্বংস করে সৃষ্টির জন্য, / নিন্দ্রিত শিবে লাথি মার আজ, / ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা, / পিয়াও এবার-অ-শিব গরল / নীলের সঙ্গে লাল মেশা। [...]
শ্বেত-শত দল-বাসিনী নয় আজ / রক্তাম্বরধারিণী মা, / ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর / সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।
‘আগমনী’ কবিতায়ও ধ্বংসের পরে সৃষ্টির কামনা দুর্গার কাছে,
ভুলে যাও শোক- চোখে জল ব’ক / শান্তির আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক। / ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক। / মা’র আবাহন-গীত চলুক।
‘ধূমকেতু’ কবিতায় ধূমকেতুরূপে কবি আবির্ভূত হয়েছেন বিপ্লবের ও ধ্বংসের প্রতীক রূপে,
আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু / স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু। / পরিণামে সৃষ্টিই উদ্দেশ্য, / আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে, / স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে তারে গ্রাসে।’ (‘ধূমকেতু’)
আবার ‘কামাল পাশা’, ‘আনোয়ার’, ‘রণ-ভেরী’, ‘শাত-ইল-আরব, ‘কোরবানী’, ‘খেয়া-পারের তরণী’ ও ‘মোর্হরম’ কবিতায় তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মিথ-পুরাণের প্রসঙ্গ-চরিত্রে শক্তি-সাহস ও বীরত্ব সন্ধান করেছেন। অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব কবিতা রচিত, অবশ্য তাতে কবির রোমান্টিক অনুভব ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং শিল্পপ্রযতœ সমান সক্রিয় ছিল।
‘কামাল পাশা’ কবিতায় সাকারিয়ার যুদ্ধে? কামাল পাশার বিজয়ে উল্লসিত কবি, সে উল্লাস নিজ দেশের তরুণদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতেই কবিতাটি সৃষ্টির লক্ষ্য, যেন তারাও কামাল পাশার মতো বীর বিক্রমে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে। তার কাছে স্বাধীন দেশ বেহেশতের চেয়েও প্রিয়, আকাক্সিক্ষত। যুদ্ধে জয়ী তুর্কী সৈনিকের কণ্ঠ যেন নজরুলের কণ্ঠই।
আজ স্বাধীন এদেশ! আজাদ মোরা বেহেশতও না চাই / বেহেশতও না চাই।’
আবার ‘আনোয়ার’ কবিতায় নিষ্ক্রিয় মুসলমানকে ‘জানোয়ার’ বলে অভিহিত করেছেন,
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার। [...]
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার। / বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার।
‘শাত-ইল-আরব’ কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের পরাধীনতার দুর্দশার করুণ চিত্র এবং সেই দুর্দশা থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে ‘রণ-ভেরী’ কবিতায়। ‘কোরবানী’ ও ‘মোর্হরম’ কবিতায় শক্তি ও ত্যাগের স্পৃহা জাগাতে চেয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে। ‘খেয়া-পারের তরণী’ কবিতায় রূপক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে আদর্শবাদী, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব আকাক্সক্ষা করেছেন, যে নেতৃত্ব জনগণকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে পারবে। এ নেতৃত্বই পাকা মাঝির মতো গভীর সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবেলা করে যাত্রীদের পাড়ে নেবার মতো জনগণকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারে,
আবু বকর ওসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারী গান- লা শরীক আল্লাহ্।
হিন্দু বা মুসলিম যে মিথ-ঐতিহ্য বা ইতিহাস ও চরিত্র নিয়েই কবিতা লিখুন না কেন, তাতে তার লক্ষ্য ছিল জনজাগরণ, আর সে জাগরণের লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের প্রধান দু’সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সংঘবদ্ধ হয়ে দেশোদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তল্পী-তল্পা নিয়ে পালাতে বাধ্য হবে।
মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি চেতনা জাগাতে, কবিতাকে সর্বজনীন করতে এবং সর্বোপরি কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে তিনি অবাধে অকৃপণভাবে হিন্দু-মুসলিম পুরাণ ও পুরাণ-প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন; এর পাশাপাশি দু’এক জায়গায় খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের মিথ-পুরাণ-প্রসঙ্গও ব্যবহার করেছেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় এ চার ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় মিশ্র মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ব্যবহারসুলভ; অন্যদিকে ‘আগমনী’, ‘ধূমকেতু’, ‘রক্তাম্বরধারিণী মা’ কবিতায় শুধু হিন্দু মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্য এবং ‘খেয়া-পারের তরণী’, ‘কোরবানী’ ও ‘মোর্হরম’ কবিতায় দু’-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলিম মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ব্যবহার করেছেন। আবার ‘কামাল পাশা’, ‘আনোয়ার’, ‘রণ-ভেরী’ ও ‘শাত-ইল-আরব’ কবিতায় সঙ্গত কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ ব্যবহৃত।
অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি কবিতায়ই ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ-আশ্রয়ে যুগ ও যুগোত্তীর্ণ বাণীর অপূর্ব শিল্পরূপ। বাংলা সাহিত্যে তাই অগ্নি-বীণা চিরস্থায়ী আসন লাভের অধিকারী।
আরো সংবাদ
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা